বাংলা নাটকের উৎস সন্ধানে
মিজানুর রহমান | প্রকাশিত: ৫ জানুয়ারী ২০২৫, ১২:৪৯
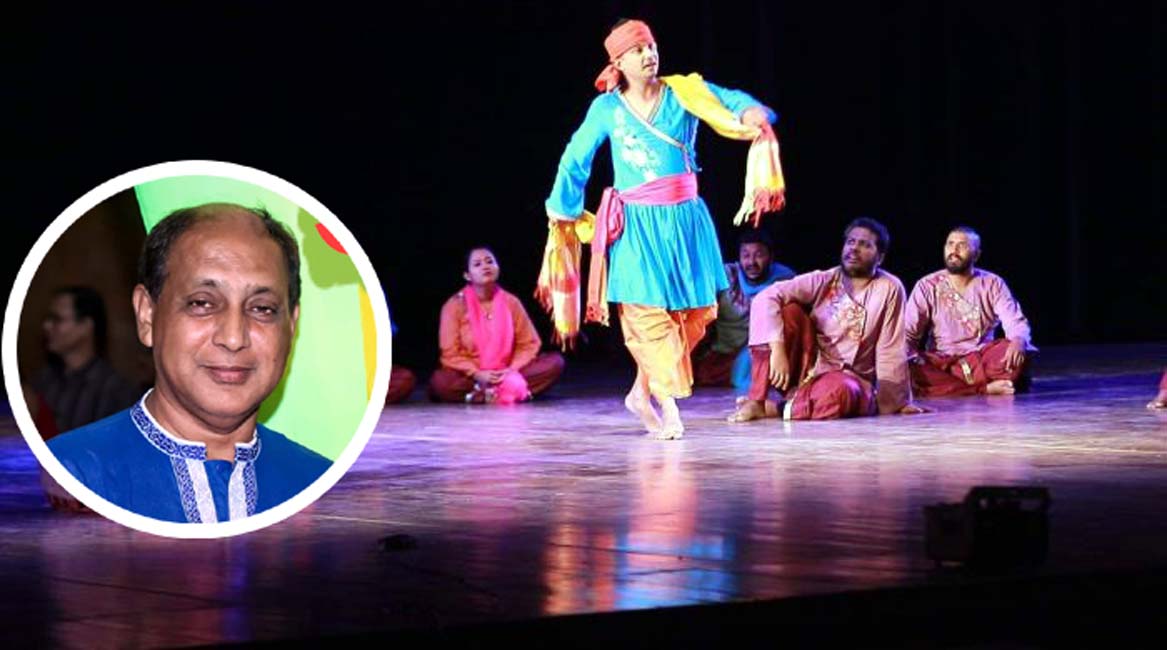
সংস্কৃতি মানব ইতিহাসের সমবয়সী। যুগের পরিবর্তনের সঙ্গে সংস্কৃতির গতিপ্রকৃতি রুপান্তরিত হয়েছে। দীর্ঘ সময় ধরে ইংরেজি কালচার শব্দের বাংলা রুপ কৃষ্টি হিসেবে প্রচলিত ছিল। উনবিংশ শতাব্দীতে অনীল চট্টপাধ্যায় কালচারের আরও সুনির্দিষ্ট বাংলা সংস্কৃতি প্রস্তাব করলে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তার অনুমোদন দেন। সেই থেকে সংস্কৃতি শব্দটি সার্বজনীন ভাবে ব্যবরিত হচ্ছে। এই সংস্কৃতির একটি গুরুত্বপূর্ণ শাখা নাটক বা থিয়েটার।
আমাদের থিয়েটারের ইতিহাসও হাজার বছরের তবে তা ছিল লোকজ আঙ্গিকে গল্প কথন আর বয়ানের ঢঙ্গে। কালের বিবর্তনে ইউরোপীয় ধারার প্রসেনিয়াম থিয়েটারে আমরা প্রবেশ করি।
বাংলা ভাষায় আধুনিক ধারার প্রসেনিয়াম থিয়েটারে যাত্রা শুরু হয় বিশিষ্ট নাট্যপ্রেমী রাশিয়ান নাগরিক -গেরাসিম স্তেফানভিচ লিয়েবেদেফ, লেবেদেফ নামে যিনি সবচেয়ে বেশি পরিচিত তার হাত ধরে। তৎকালীন সোভিয়েত ইউনিয়নের ইউক্রেনে জন্মে ছিলেন এই গুণী। তাঁর হাত ধরেই কোলকাতায় প্রসেনিয়াম বাংলা থিয়েটারের পত্তন হয়।
লেবেদেফ রাশিয়া থেকে ইংল্যান্ড হয়ে ভারতের মুম্বাই বর্তমানে চেন্নাই শহরে আসেন,সেখানে তার ভালো না লাগলে পশ্চিম বঙ্গের কোলকাতা এসে থিতু হোন। প্রথমে তিনি সংগীত নিয়ে কাজ শুরু করে পাশাপাশি বাংলা শিখেছিলেন। কোলকাতায় তখন বিনোদন ধারার নাটক ও ইংরেজদের মনোরঞ্জনে ইংরেজি নাটক হতো।
সেই সময়ে লেবেদেফ নিয়মিত বাংলা নাটক করার লক্ষ্যে মনঃস্থির করে মলিয়ের এর -”লাভ ইজ পাওয়ার “ ও রিচার্ড পল জড্রেল এর - “ দি ডিজগাস” নাটকের বাংলা রুপান্তর করেন। কিন্তু ইংরেজদের মঞ্চে নাটক করার কোন অনুমতি না পেয়ে নিজ উদ্যোগে ১৭৯৫ সালের ১ জুন থেকে ৬০ টাকা মাসিক ভাড়ায় ২৫ নং ডোমতলা ষ্ট্রিট বর্তমানে এজরা ষ্ট্রিটে জগন্নাথ গাঙ্গলীর বাড়ি ভাড়া নিয়ে তিন মাসের মধ্যেই গড়ে তুললেন আধুনিক দোতলা নাট্যশালা।
আলপনা, মঙ্গলঘট ও কসাগা ইত্যাদি দিয়ে তিনি মঞ্চ সাজিয়ে ছিলেন। ইউরোপিয়ান প্রসেনিয়াম থিয়েটারের আদলে তৈরী এই নাট্যমঞ্চে বক্স ও পিট গ্যালারি ছিল। লেবেদেফ এর বেঙ্গলী থিয়েটারে প্রথম বাংলা নাটক ছিল রিচার্ড পল জড্রেল এর দি ডিজগাসের বাংলারুপ-”কাল্পনিক সংবদল”। প্রথম প্রদর্শনী হয়েছিল ১৭৯৫ সালের ২৭ নভেম্বর দর্শক উপস্থিত ছিলেন ২০০ জন। দ্বিতীয় প্রদর্শনী ছিল ১৭৯৬ সালের ২১ মার্চ,দর্শক উপস্থিত ছিলেন ৩০০ জন।
এই সাফল্যে লেবেদেফ উৎসাহী হয়ে তৃতীয় প্রদর্শনীর সকল আয়োজন সম্পন্ন করে প্রচারের জন্য পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দেন। এমতাবস্থায় অকস্মাৎ আগুনে পুড়ে শেষ হয়ে যায় বেঙ্গলী থিয়েটার। ইংরেজদের অপছন্দের কারণেই সেটি হয়েছিল বলে ধারণা করা হয়। এর ফলে তিনি ভারত ছেড়ে যেতে বাধ্য হোন।
উনিশ শতকে আরও কিছু থিয়েটার প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলো যেমন হিন্দু থিয়েটার ১৮৩১ সাল,ওরিয়েন্টাল থিয়েটার ১৮৫৩ সাল,জোড়াসাঁকো নাট্যশালা ১৮৫৪ সাল,বিদ্যোৎসাহিনী মঞ্চ ১৮৫৭ সাল। এইসব থিয়েটারে ইংরেজদের পছন্দে হাল্কা রসবোধে নানা দেবদেবীর প্রশংসা মূলক নাটক মঞ্চায়ন হতো। সে সময় পাঁচ অংকের দীর্ঘ নাটক সারারাত ধরে অভিনীত হতো।
বাঙালির বিনোদনে সংগীত খুবই জনপ্রিয় ধারা তাইতো প্রায় সকল নাটকেই সংগীতের ব্যবহার হতো গুরুত্বসহ। এই সময় ইংরেজরা ও তাদের অনুগত জমিদারগন এই ধারার নাটক কে প্রশ্রয় দিতো। প্রচলিত এই ধারার বাইরে এসে দীনবন্ধু মিত্র ১৮৬০ সালে লেখেন জীবন ঘনিষ্ঠ নাটক নীলদর্পণ। সেই বছরে ঢাকার পুর্ববাংলা নাট্যমঞ্চে টিকেটের বিনিময়ে অভিনীত হয় নীলদর্পণ নাটক। ১৮৭২ সালে কোলকাতায় ন্যাশনাল থিয়েটারের উদ্বোধনী নাটক ছিল নীলদর্পণ।
১৮৭৩ সালে মঞ্চে পাকাপাকি ভাবে অভিনেত্রী গ্রহনের ফলে নানান তিক্ততা তৈরী হয়। বারাঙ্গনা পল্লী থেকে আনা এইসব অভিনেত্রীর কারণে মঞ্চ একেবারে অপবিত্র ও দুষিত হয়ে পড়েছে এই ধারণায় শিক্ষিত রুচিশীল দর্শক মঞ্চ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়। সাধারণ দর্শক ও কিছু পয়সাওয়ালা বাবু সম্প্রদায়ের লোক তাদের আমোদ-ফুর্তির জায়গা হিসেবে এখানে স্হায়ী হয়। পরবর্তীতে দেবদেবীর কাহিনী, যাত্রারস,ধর্মাশ্রয়ী আবেগ তাড়িত গল্পের কারণে মহিলা দর্শকও যুক্ত হয়।
যারা দুঃখ থেকে হাসি-কান্নায় বিভোর, ধর্মবোধে দেবদেবীর অলৌকিকতায় বিশ্বাসী ও ভক্তিভাবে আবেগাপ্লুত তারাও নাটকে যেতো। এমতাবস্থায় ১৮৭৬ সালে আসে অভিনয় নিয়ন্ত্রণ আইন। বাংলা নাটকের স্বাধীন ভাবনাকে আরও নিয়ন্ত্রণ করে দিলো।
ব্রিটিশ বিরোধী কোনো নাটকেরই মঞ্চাভিনয়ের অনুমতি রইলো না বরং রইলো শাস্তি ও জরিমানার ভয়। এর ফলে জাতীয় ভাবোদ্দীপক ও স্বদেশানুরাগের নাটক লেখা, অভিনয় করা বন্ধ হয়ে গেলো। তারপর থেকে ব্যবসায়ি রঙ্গমঞ্চ তার দর্শক চাহিদার কথা বিবেচনায় নিয়ে বিনোদনধর্মী প্রযোজনা করতে থাকলো।
উনিশ শতকের শেষের দিকে ঢাকায় কিছু নাট্যমন্ঞ্চ নির্মিত হলো যেমন- পুর্ববঙ্গ রঙ্গভূমি ১৮৬৫ সালে,ক্রাউন থিয়েটার মঞ্চ ১৮৯০-৯২ এর মধ্যে, ডায়মন্ড জুবিলি থিয়েটার ১৮৯৭ সালে ইত্যাদি। এই সময় মুন্সিগঞ্জে নির্মাণ হয় জগদ্ধাত্রী নাট্যমঞ্চ। এই সকল মঞ্চে কোলকাতা অনুকরণে বিনোদন ধারার নাটকই হতো।
১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ প্রতিরোধের আন্দোলনের জোয়ারে মঞ্চ গুলোতে আবারও স্বদেশ প্রেম ও জাতীয় ভাবানুবাগের বিষয়ে নাটক মঞ্চায়ন শুরু হলো। আইন উপেক্ষা করেই স্বদেশ প্রেমের নাটক করতে লাগলো। গিরিশ চন্দ্র,ক্ষীরোদ প্রসাদ, দ্বিজেন্দ্র লাল তাদের ঐতিহাসিক নাটক গুলোতে সমসাময়িক ভাবনা,জাতীয়তাবোধ,হিন্দু-মুসলমান সম্প্রীতি ও স্বাধীনতার জয়গান গাইলেন।
দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ আর ১৯৪৩ সালের দুর্ভিক্ষে নিষ্পেষিত মানুষের পাশে দাড়াতে ও ব্রিটিশ বিরোধী সংগ্রামকে শানিত করতে ভারতীয় গণনাট্য সংঘ বিজন ভট্টাচার্যের লেখা নবান্ন নাটক নিয়ে আসলেন মঞ্চে ১৯৪৪ সালে। সেই নাটকে ছিলেন অহিন্দ্র চৌধুরী, শম্ভু মিত্র, তৃপ্তি মিত্র আরও গুরুত্বপূর্ণ অনেকে। রাজনৈতিক টানাপোড়েনে ভারতীয় গণনাট্য সংঘ বিভক্তিতে পড়ে আর শম্ভু মিত্র, তৃপ্তি মিত্র বের হয়ে এসে বহুরুপী নামে নতুন দলগঠন করেন।
সে সময়ে আরও কিছু দল গঠিত হয়। সমান্তরাল ভাবে কাজ করতে থাকেন শম্ভু মিত্র, তৃপ্তি মিত্র, অজিতেশ বন্দ্যোপাধায়,উৎপল দত্ত, বাদল সরকারসহ আরও অনেকে।
১৯৪৭ সালের দেশভাগে পুর্ববাংলার মানুষ হতাশ হয়েছিলেন। অন্যায্য ও বৈষম্য মুখ্য হয়ে উঠে। শুরু হয়ে যায় ভাষার লড়াই। ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারীর কারণে অনেককেই সরকার কারাবন্দী করে। মুনীর চৌধুরী ছিলেন প্রগতি লেখক সংঘের সাধারণ সম্পাদক আর সে কারণে তাকে কারাবন্দী করা হয়েছিল। সেখানে থেকেই তিনি লেখেন কবর নাটক আর ১৯৫৩ সালের ২১ ফেব্রুয়ারী কারাগারে সে নাটক অভিনীত হয়েছিল।
১৯৫৬ সালের ৯ মে পাকিস্তানের সংবিধান রচিত হলে পুর্ববঙ্গের মানুষ সংক্ষব্ধ হয়। সে সময়ের নানা রাজনৈতিক তৎপরতার পাশাপাশি এপার বাংলার প্রথম গ্রুপ থিয়েটার ড্রামা সার্কেল গঠিত হয়। আসকার ইবনে শাইখ, নুরুল মোমেন,মাসুদ আলী খান মোহাম্মদ সাজ্জাদ হোসেন মিলে দল গঠন করেন। সৈয়দ ওয়ালী উল্লাহ তখন লন্ডন থেকেও তার সাথে যুক্ত ছিলেন।
১৯৬৪ সালে মুনীর চৌধুরীর লেখা রক্তাত প্রান্তর নাটকের মাধ্যমে রামেন্দু মজুমদার, নুরজাহান মুর্শেদ,লিলি চৌধুরী ও ফেরদৌসী মজুমদার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীক নাটকে যুক্ত হোন। সে সময় সৃজনী তে কাজ করতেন কামাল লোহানী তিনি ম্যাক্সিম গোর্কি মা নাটকে অভিনয় করেছিলেন। ১৯৬৯ সালে উদীচী শিল্পীগোষ্ঠী “আলো আসবে” নাটক করে।
১৯৬৮ সালে ফজলে লোহানীর বাসায় জিয়া হায়দার আর আতাউর রহমানের নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলো নাগরিক নাট্যসম্প্রদায়। ১৯৬৯ সালে খেয়ালী নাট্যগোষ্টি বরিশাল। ১৯৭১ সালে মামুনুর রশীদ এর নেতৃত্বে আরণ্যক, ১৯৭২ সালে রামেন্দু মজুমদারের থিয়েটার, ম. হামিদের নাট্যচক্র,১৯৭৩ সালে নাসির উদ্দীন ইউসুফের নেতৃত্বে ঢাকা থিয়েটার।
প্রায় কাছাকাছি সময়ে চট্টগ্রামসহ আরও অন্যান্য জায়গায় বেশকিছু দল গঠিত হলে স্বাধীন বাংলায় নাট্যচর্চার জাগরণ তৈরী হয়। সত্তর ও আশির দশকে সারাদেশে নবচেতনার গ্রুপ থিয়েটার চর্চার বিস্তারে একটি জাতীয় ভিত্তিক মোর্চা গঠনের তাগিদ অনুভূত হয় আর তারই ফলশ্রুতিতে গঠিত হয় বাংলাদেশ গ্রুপ থিয়েটার ফেডারেশান।
১৯৮০ সালের ২৯ নভেম্বর প্রতিষ্ঠিত এই সংগঠনের সভাপতি ছিলেন রামেন্দু মজুমদার ও সাধারণ সম্পাদক ছিলেন নাসির উদ্দীন ইউসুফ। সেই থেকে বাংলাদেশ গ্রুপ থিয়েটার ফেডারেশান নাটকের অভিভাবকত্ব করছে।
সম্পাদনা : রাহুল রাজ




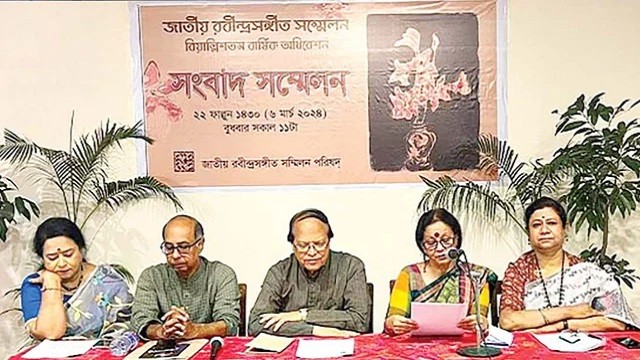


পাঠকের মন্তব্য
মন্তব্য পাঠকের একান্ত ব্যক্তিগত। এর জন্য সম্পাদক দায়ী নন।