বদলে যাচ্ছে মুক্তিযোদ্ধার সংজ্ঞা!
রাজীব রায়হান | প্রকাশিত: ১৬ ডিসেম্বর ২০২৪, ১৬:৫৫

কালের কণ্ঠের প্রধান শিরোনাম, 'বদলে যাচ্ছে মুক্তিযোদ্ধার সংজ্ঞা!'। প্রতিবেদনে বলা হচ্ছে, মুক্তিযুদ্ধের ৫৩ বছর পর বীর মুক্তিযোদ্ধাদের সংজ্ঞায় আরেকবার পরিবর্তন আসতে পারে। প্রস্তাবিত নতুন সংজ্ঞা অনুযায়ী, মুক্তিযুদ্ধে সরাসরি অংশগ্রহণকারীরাই হবেন বীর মুক্তিযোদ্ধা।
অন্যদিকে বিশ্ব জনমত গঠনে ভূমিকা রাখা ব্যক্তিরা, মুজিবনগর সরকারের কর্মকর্তা-কর্মচারী, চিকিৎসাসেবা প্রদানকারী, শিল্পীসমাজসহ যারা মুক্তিযুদ্ধে বিভিন্নভাবে সহায়তা করেছেন তাদের 'যুদ্ধ সহায়ক' করার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। একই সঙ্গে মুক্তিযোদ্ধা হওয়ার সর্বনিম্ন বয়সেও পরিবর্তন আসতে পারে। মুক্তিযোদ্ধাদের সর্বনিম্ন বয়স হতে পারে ১৩ বছর। ২০২২ সালের জাতীয় মুক্তিযোদ্ধা কাউন্সিল (জামুকা) আইন সংশোধন করে অধ্যাদেশ করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।
মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক উপদেষ্টা ফারুক ই আজমের মতে জামুকার আইনে কিছু দলীয় ন্যারেটিভ আছে। এটা নৈর্ব্যক্তিক একটা অবস্থান থেকে হওয়া উচিত বলে তিনি মনে করেন। স্বাধীনতার পর ১৯৭২ সালে প্রথম মুক্তিযোদ্ধার সংজ্ঞা নির্ধারণ করা হয়। সেই সংজ্ঞায় মুক্তিযুদ্ধে মুক্তিবাহিনীর সদস্য হিসেবে যারা দায়িত্ব পালন করেছেন তাদেরই মুক্তিযোদ্ধা বলা হয়েছে। পরে ২০১৬ সালে বিগত আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে এক গেজেটের মাধ্যমে মুক্তিযোদ্ধার নতুন সংজ্ঞা নির্ধারণ করে ।
ওই সংজ্ঞায় রণাঙ্গনের যোদ্ধাদের পাশাপাশি বিশ্বজনমত গঠনে সক্রিয় ভূমিকা পালনকারী বাংলাদেশি নাগরিক, মুজিবনগর সরকারের অধীন কর্মকর্তা-কর্মচারী-দূত, নির্যাতিতা বীরাঙ্গনা, স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের শিল্পী ও কলা-কুশলী, দেশ ও দেশের বাইরে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে দায়িত্ব পালনকারী বাংলাদেশি সাংবাদিক, আহত মুক্তিযোদ্ধাদের চিকিৎসাসেবা দেওয়া মেডিক্যাল টিমের ডাক্তার, নার্স ও সহকারী, এমনকি স্বাধীন বাংলা ফুটবল দলের খেলোয়াড় মুক্তিযোদ্ধা বলা হয়েছে।
তবে নতুন খসড়ায় তাদেরকে 'যুদ্ধ-সহায়ক' নাম দিয়ে শ্রেণিভুক্ত করার চিন্তা করা হচ্ছে। স্বাধীনতার এত বছর পরও মুক্তিযোদ্ধার সংজ্ঞা ও তালিকা চূড়ান্ত না করতে পারায় হতাশা ও ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন বীর মুক্তিযোদ্ধা ও বিশিষ্টজনরা।
দ্য ডেইলি স্টারের প্রধান শিরোনাম, 'The day a nation cried tears of joy' অর্থাৎ 'যেদিন জাতি কেঁদেছিল আনন্দের অশ্রু'। প্রতিবেদনে একাত্তরের ডিসেম্বরের স্বাধীনতার যে হাওয়া বইছিলো এবং চূড়ান্ত বিজয় অর্জনের আগে ইতিহাসের নানা পরিক্রমার কথা তুলে ধরা হয়েছে।
১৯৭১ সালের ডিসেম্বরের শুরু থেকেই পাকিস্তান নিয়ন্ত্রণ হারাতে থাকে মুক্তিবাহিনী ও ভারতীয় সেনাবাহিনীর যৌথ আক্রমণে বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চল শত্রুমুক্ত হয়। গেরিলা যোদ্ধারা ঢাকায় প্রবেশ করে এবং ১৩ই ডিসেম্বরের মধ্যে মানিকগঞ্জ ও নারায়ণগঞ্জ মুক্ত হয়। ১৪ই ডিসেম্বর, ভারতীয় বিমানবাহিনী গভর্নরের বাসভবনে হামলা চালায়, যার ফলে পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর ড. এম এ মালিক পদত্যাগ করেন।
১৫ই ডিসেম্বর পাকিস্তান যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব দেয়, আর জাতিসংঘ ও পোল্যান্ড শান্তির আহ্বান জানায়। তবে জাতিসংঘে জুলফিকার আলি ভুট্টো এ প্রচেষ্টাকে তীব্রভাবে নিন্দা করেন। ওইদিন গাজীপুর মুক্ত হয়, এবং ঢাকায় পাকিস্তানি সেনারা ঘেরাও হয়ে পড়ে। এরপর ভারতীয় ও মিত্রবাহিনী আনুষ্ঠানিক আত্মসমর্পণের প্রস্তুতি নেয়।
১৬ই ডিসেম্বর ভারতীয় সেনাবাহিনীর জেনারেল জ্যাকব ঢাকায় আসেন আত্মসমর্পণের নথি নিয়ে। পাকিস্তানি জেনারেলরা ভাবছিলেন তারা যুদ্ধবিরতির আলোচনা করছেন, কিন্তু তাদের আত্মসমর্পণের শর্ত দেওয়া হয়।
অবশেষে, লেফটেন্যান্ট জেনারেল নিয়াজি ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে জনসমক্ষে আত্মসমর্পণের নথিতে সই করেন। তিনি প্রতীকীভাবে তার রিভলভার জেনারেল অরোরার হাতে তুলে দেন। আত্মসমর্পণের খবর ছড়িয়ে পড়তেই সারাদেশে বিজয়ের আনন্দ শুরু হয়।
ঢাকার রাস্তাগুলো উল্লসিত জনতায় ভরে যায়, আর রেসকোর্স ময়দান জনসমুদ্রে পরিণত হয়। স্বাধীনতার এই বিশেষ মুহূর্তে অনেকেই আনন্দে কেঁদে ফেলেন। ১৬ই ডিসেম্বর ১৯৭১ সালে পাকিস্তানের আনুষ্ঠানিক আত্মসমর্পণের মাধ্যমে দীর্ঘ সংগ্রামের পর বাংলাদেশ স্বাধীন দেশ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়।
প্রথম আলোর প্রধান শিরোনাম, 'মুক্তিযুদ্ধ সর্বোচ্চ গৌরবের, চব্বিশ তার ধারাবাহিকতা'। প্রতিবেদনে একজন মুক্তিযোদ্ধা ও গণঅভ্যুত্থানের দুজন সংগঠকের আলাপচারিতায় উঠে এল মুক্তিযুদ্ধ ও গণ-অভ্যুত্থানের প্রেক্ষাপট ও আকাঙ্ক্ষার কথা।
মুক্তিযোদ্ধা জানিয়েছেন যে কীভাবে তিনি পাকিস্তান থেকে পালিয়ে এসেছেন, কীভাবে মুক্তিযুদ্ধে যোগ দিলেন, কী স্বপ্ন ছিল— তবে তিনি যে আকাঙ্ক্ষা নিয়ে মুক্তিযুদ্ধ করেছিলেন, তা অনেকাংশে পূরণ হয়নি বলে দাবি করেন।
অন্যদিকে গণ-অভ্যুত্থানের দুই সংগঠক জানায়, মুক্তিযুদ্ধের আকাঙ্ক্ষা পূরণ হয়নি বলেই চব্বিশে তাদের রাস্তায় নামতে হয়েছে। গণতান্ত্রিক বাংলাদেশ, সাম্য ও মানবিক মর্যাদা প্রতিষ্ঠার জন্য লড়াই চলবে।
তারা আরও বলেন, মুক্তিযুদ্ধ বাংলাদেশের মানুষের জন্য সর্বোচ্চ গৌরবের। একাত্তর ও চব্বিশ মুখোমুখি করার মতো বিষয় নয়; বরং চব্বিশের গণ-অভ্যুত্থান একাত্তরের ধারাবাহিকতা। ঘণ্টা দেড়েক কথোপকথন শেষে বীর মুক্তিযোদ্ধা ও চব্বিশের গণ-অভ্যুত্থানের দুই সংগঠক এগিয়ে গেলেন স্মৃতিসৌধের দিকে। খালি পায়ে হাঁটলেন তারা। একপর্যায়ে তাঁরা তিনজন একসঙ্গে স্যালুট জানান একাত্তরে দেশের জন্য প্রাণ উৎসর্গকারীদের। সব শেষে তারা ছবি তোলেন জাতীয় স্মৃতিসৌধের একটি স্মৃতিফলকের সামনে দাঁড়িয়ে।
মানবজমিনের প্রধান শিরোনাম, 'দূষণে ধুঁকছে ঢাকা, বাড়ছে রোগ-বালাই'। প্রতিবেদনে বলা হচ্ছে, ঢাকার বায়ুদূষণ ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে, যা জনস্বাস্থ্যের ওপর গুরুতর প্রভাব ফেলছে। ধুলাবালি, যানবাহনের ধোঁয়া, কলকারখানার নির্গমন, নির্মাণকাজ এবং বর্জ্য পোড়ানোর কারণে বাতাসের মান 'অস্বাস্থ্যকর' থেকে 'খুবই অস্বাস্থ্যকর' পর্যায়ে রয়েছে।
গত এক মাসে আইকিউএয়ার সূচকে ঢাকার বায়ুমান কখনোই 'স্বাস্থ্যকর' স্তরে ওঠেনি। নারায়ণগঞ্জ, গাজীপুরসহ আশেপাশের জেলাগুলোতেও একই অবস্থা বিরাজ করছে। বায়ু দূষণের পেছনে মূল যেসব কারণকে চিহ্নিত করা হয়েছে সেগুলো হলো: মেট্রোরেল ও এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ের মতো মেগা প্রকল্পের নির্মাণ, বর্জ্য ব্যবস্থাপনার অভাব, ইটভাটা ও ফিটনেসবিহীন যানবাহনযত্রতত্র আবর্জনা পোড়ানো।
বায়ুদূষণের কারণে শ্বাসকষ্ট, হাঁপানি, নিউমোনিয়া, ফুসফুসের ক্যান্সারসহ বিভিন্ন রোগ বাড়ছে। শিশু, বয়স্ক, এবং দীর্ঘমেয়াদি রোগে আক্রান্ত ব্যক্তিরা সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। ২০২১ সালে বাংলাদেশে বায়ুদূষণের কারণে দুই লাখ ৩৫ হাজার মানুষ মারা গেছে, যার মধ্যে ১৯ হাজার ছিল পাঁচ বছরের নিচে শিশু।
জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞদের মতে, বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণে নির্মাণকাজে নিয়ম মানা, ফিটনেসবিহীন যানবাহন বন্ধ করা, ইটভাটা সরিয়ে নেয়া, এবং বর্জ্য ব্যবস্থাপনাকে সুসংগঠিত করা জরুরি।
দেশ রূপান্তরের প্রধান শিরোনাম, 'র্যাব বিলুপ্তির পর কী'। প্রতিবেদনে বলা হচ্ছে, নারায়ণগঞ্জে সাত খুনের ঘটনার পর বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়া 'র্যাব' বিলুপ্তির দাবি তুলেছিলেন, যা পরবর্তীতে বিচারবহির্ভূত হত্যা, গুম, এবং মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগে দেশে-বিদেশে আরও জোরালো হয়।
২০২১ সালে যুক্তরাষ্ট্র র্যাবের কিছু কর্মকর্তার ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করলে র্যাবের কার্যক্রম অনেকটা সীমিত হয়। বর্তমানে, ছাত্র-জনতার আন্দোলন এবং বিভিন্ন সংস্থার সুপারিশে র্যাব বিলুপ্তির আলোচনা আবার তীব্র হয়েছে।
বিএনপি পুলিশ সংস্কার কমিশনে র্যাব বিলুপ্তির প্রস্তাব দিয়েছে এবং সরকারের গুম তদন্ত কমিশনও এ বাহিনী বিলুপ্তির পক্ষে সুপারিশ করেছে। নিরাপত্তা বিশ্লেষকরা র্যাবের বিকল্প একটি শক্তিশালী বাহিনী গঠনের প্রস্তাব দিয়েছেন, তবে তারা সতর্ক করেছেন যে এতে রাজনৈতিক প্রভাব পরিহার করতে হবে।
র্যাবের বর্তমান মহাপরিচালক বলেছেন, তারা সরকারের সিদ্ধান্ত মেনে চলবেন এবং সুষ্ঠু তদন্ত ও বিচারের মাধ্যমে দায়মুক্তি চান। র্যাব ২০০৪ সালে সন্ত্রাস দমনের জন্য গঠিত হলেও বিলুপ্তির পর দেশীয় নিরাপত্তা ব্যবস্থার ভারসাম্য বজায় রাখতে বিকল্প বাহিনী গঠন জরুরি বলে বিশেষজ্ঞরা মনে করেন। তবে সন্ত্রাস দমনে নতুন কোনো বাহিনী গঠন হলে সেখানে যদি রাজনৈতিক বিবেচনায় লোকজন নেওয়া হয় তাহলে কোনো সুফল আসবে না বলে তারা জানান।
সমকালের প্রধান শিরোনাম, ''বঞ্চিত' ৭৬৪ কর্মকর্তা পদের সঙ্গে পাবেন আর্থিক সুবিধা'। প্রতিবেদনে বলা হচ্ছে, অন্তর্র্বতী সরকার আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে অবসরে যাওয়া ৭৬৪ জন 'বঞ্চিত' কর্মকর্তাকে পদমর্যাদা ও আর্থিক সুবিধা দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এ উদ্যোগে সরকারের প্রাথমিক ব্যয় হবে অন্তত ৬৮ কোটি টাকা। এই কর্মকর্তারা ভূতাপেক্ষ পদোন্নতি পাবেন, যা নিয়ে প্রশাসনে মিশ্র প্রতিক্রিয়া তৈরি হয়েছে।
এই উদ্যোগের আওদায় সচিব পদে ১১৯ জন, গ্রেড-১ পদে ৪১ জন, অতিরিক্ত সচিব ৫২৮ জন, যুগ্ম সচিব ৭২ জন, ও উপসচিব ৪ জনসহ ৭৬৪ জন কর্মকর্তাকে ভূতাপেক্ষ পদোন্নতি দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। এখানে তাদের আর্থিক সুবিধাও দেয়া হবে।
পর্যালোচনা কমিটি নয় জনকে চার ধাপ, ৩৪ জনকে তিন ধাপ, ১২৬ জনকে দুই ধাপ, এবং ৫৯৫ জনকে এক ধাপ পদোন্নতির সুপারিশ করেছে। তবে প্রশাসনিক বিশেষজ্ঞরা সততা ও দক্ষতার ভিত্তিতে পদোন্নতি দেয়ার পক্ষে মত দিয়েছেন। তাদের আশঙ্কা এ উদ্যোগ ভবিষ্যতে অপব্যবহারের দিকে ঠেলে দিতে পারে।
১০ই ডিসেম্বর কমিটি প্রধান উপদেষ্টার কাছে এ সংক্রান্ত প্রতিবেদন পেশ করলেও তা এখনও মন্ত্রণালয়ে ফেরত আসেনি। এদিকে ক্ষুব্ধ কর্মকর্তারা সচিবালয়ে অবস্থান নিয়ে দ্রুত প্রজ্ঞাপন জারির দাবি জানিয়েছে। এ নিয়ে জনপ্রশাসন সচিবের সাথেও তাদের আলোচনা হয়। দাবিগুলো দ্রুত বাস্তবায়ন না হলে কঠোর আন্দোলনের হুমকি দিয়েছেন কর্মকর্তারা। এ উদ্যোগের মাধ্যমে প্রথমবারের মতো এত বড় সংখ্যক অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তার পদমর্যাদা পুনর্বিন্যাস করা হচ্ছে, যা প্রশাসনের জন্য গুরুত্বপূর্ণ দৃষ্টান্ত স্থাপন করবে।
বণিক বার্তার প্রধান শিরোনাম, 'ঋণগ্রস্ত ও রুগ্ণ টিসিবি দিয়ে বাজার স্থিতিশীল রাখা সম্ভব কি'। প্রতিবেদনে বলা হচ্ছে, ট্রেডিং করপোরেশন অব বাংলাদেশ (টিসিবি) ক্রমেই ঋণনির্ভর হয়ে পড়ছে এবং লোকসানও বাড়ছে। টিসিবি ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়ে পণ্য কেনে ও কম দামে বিক্রি করে, তবে সুদের কারণে তাদের খরচ বেড়ে যাচ্ছে।
২০২২-২৩ অর্থবছরে টিসিবির দায় ছিল তিন হাজার ৭৬৪ কোটি টাকা, যা ২০২৪-২৫ অর্থবছরে বেড়ে ১৬ হাজার ২০৩ কোটি টাকায় দাঁড়ানোর প্রাক্কলন রয়েছে। তাদের লোকসানও বেড়েছে, ২০২২-২৩ সালে এক হাজার ১৪০ কোটি টাকা থেকে ২০২৩-২৪ সালে ছয় হাজার ৩৪ কোটি টাকায় পৌঁছেছে।
সংস্থার কার্যক্রমে নগদ অর্থের সংকট রয়েছে। সরকার সময়মতো তহবিল না দেওয়ায় টিসিবি ঋণের ওপর নির্ভরশীল। এছাড়া, গুদামের অভাব ও দুর্নীতির অভিযোগে টিসিবি কার্যক্রমে কাঙ্ক্ষিত সাফল্য দেখাতে পারছে না।
টিসিবি জনগণকে সাশ্রয়ী মূল্যে তেল, চিনি, ডাল, আলু ইত্যাদি পণ্য সরবরাহ করে। তবে চাহিদা বাড়লেও তাদের সক্ষমতা কম। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, টিসিবি বাজার স্থিতিশীল রাখতে পারছে না এবং এটি নিয়ে নতুন মডেল ভাবনার প্রয়োজন।
সংবাদের প্রথম পাতার খবর, 'এলডিসি থেকে উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণ নিয়ে 'ভাবছে' অন্তর্র্বতী সরকার: প্রেস সচিব'। প্রতিবেদনে স্বল্পোন্নত দেশের তালিকা থেকে বেরিয়ে বাংলাদেশ ২০২৬ সালে উন্নয়নশীল দেশের মর্যাদা অর্জন করবে কি না, তার পরিকল্পনা ও এর সম্ভাব্য প্রভাব নিয়ে একটি সংক্ষিপ্ত চিত্র তুলে ধরা হয়েছে।
বর্তমান সামষ্টিক অর্থনীতির পরিস্থিতি ও স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উত্তরণের প্রস্তুতি বিষয়ে রোববার ঢাকায় এক কর্মশালায় ভার্চুয়ালি যুক্ত হয়ে প্রেস সচিব শফিকুল আলম এ কথা বলেন। ২০১৮ সালে বাংলাদেশ মাথাপিছু আয়, মানবসম্পদ সূচক, ও অর্থনৈতিক ভঙ্গুরতা সূচকের শর্ত পূরণ করে উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণের প্রাথমিক যোগ্যতা অর্জন করে। সব ঠিক থাকলে ২০২৬ সালের ২৪শে নভেম্বর বাংলাদেশ স্বল্পোন্নত দেশের উপরের ধাপে উত্তীর্ণ হবে।
তবে স্বল্পোন্নত দেশের তালিকা থেকে বের হয়ে গেলে ইউরোপীয় রপ্তানি বাজারে শুল্ক ও কোটামুক্ত সুবিধা হারানোর আশঙ্কা রয়েছে। অন্তর্র্বতী সরকার জাতিসংঘসহ বিভিন্ন পক্ষের সঙ্গে আলোচনা করার কথা জানিয়েছে। এক্ষেত্রে তারা সময় বাড়ানোর আবেদন করা হতে পারে বলে জানিয়েছেন তবে উত্তরণ ঠেকানো প্রায় অসম্ভব।
উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণ হলে আন্তর্জাতিক ঋণ পাওয়ার সুযোগ বাড়বে, তবে রপ্তানি সুবিধা হারালে অর্থনীতিতে চ্যালেঞ্জের মুখে পড়বে। সময় বৃদ্ধির জন্য যৌক্তিক আবেদন করা গেলে প্রস্তুতি গ্রহণের সুযোগ পাওয়া যাবে। বলা হচ্ছে, বিগত সরকারের আমলে অর্থনৈতিক ডেটা নিয়ে কারসাজির অভিযোগ রয়েছে, যার কারণে বর্তমান পরিসংখ্যানের সঠিকতা নিয়ে সন্দেহ তৈরি হয়েছে।
যুগান্তরের প্রধান শিরোনাম, 'বেক্সিমকোর দায় বিভিন্ন ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানে: পঞ্চাশ হাজার কোটি টাকা'। প্রতিবেদনে বলা হচ্ছে,বেক্সিমকো গ্রুপের মোট দেনা দেশের ১৬টি ব্যাংক ও সাতটি আর্থিক প্রতিষ্ঠানের কাছে ৫০ হাজার কোটি টাকা, যার মধ্যে ৩১ হাজার কোটি টাকা খেলাপি ঋণ। আইন লঙ্ঘন করে ৭৮টি প্রতিষ্ঠানকে এই গ্রুপ আর্থিক সুবিধা পেয়েছে।
বাংলাদেশ ব্যাংক হাইকোর্টে এ তথ্য তুলে ধরে জানিয়েছে, জনতা ব্যাংক একাই বেক্সিমকো গ্রুপকে তার প্রাপ্যের ২০ গুণ বেশি ঋণ দিয়েছে। এছাড়া, অধিকাংশ ঋণ বেনামি ছিল, যা পরে গ্রুপের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের নামে দেখানো হয়েছে।
হাইকোর্টের আদেশ অনুযায়ী, বেক্সিমকো গ্রুপের সম্পত্তি অ্যাটাচ ও রিসিভার নিয়োগের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আপিল বিভাগ বেক্সিমকো ফার্মাসিউটিক্যালসের ক্ষেত্রে রিসিভার নিয়োগের আদেশ স্থগিত করেছে।
জনতা ব্যাংকের একটি শাখা থেকেই গ্রুপটি ২৭ হাজার কোটি টাকার ঋণ নিয়েছে, যা মোট ঋণের ৬৫%। বিশ্লেষকরা মনে করেন, এই প্রক্রিয়ায় ব্যাংকের কর্মকর্তারা এবং বাংলাদেশ ব্যাংকও জড়িত, তাই নিরপেক্ষ তদন্ত ও ঋণ আদায় জরুরি।
বিষয়:





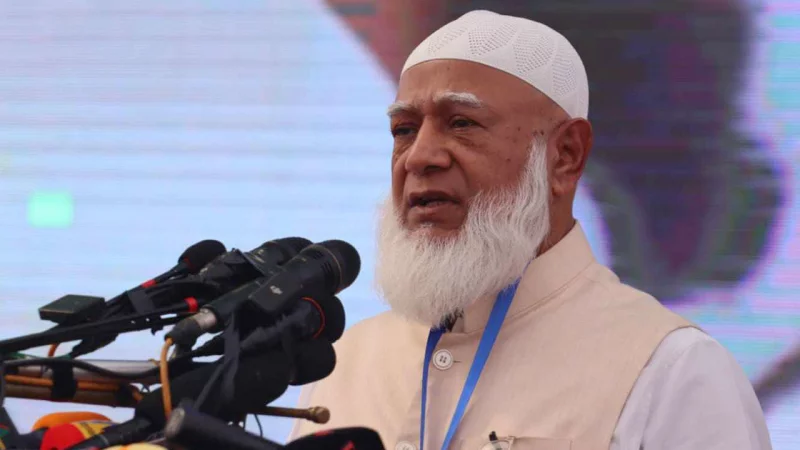
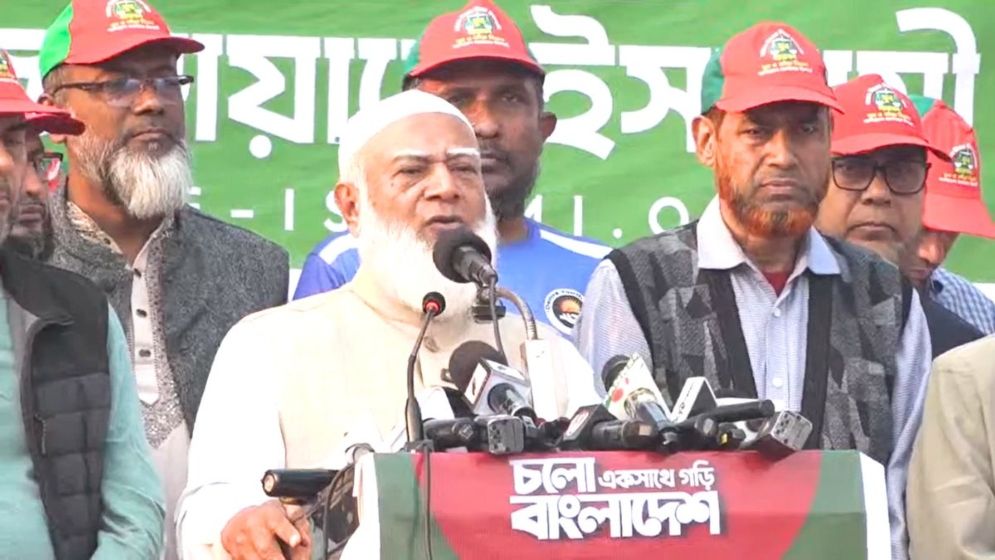
পাঠকের মন্তব্য
মন্তব্য পাঠকের একান্ত ব্যক্তিগত। এর জন্য সম্পাদক দায়ী নন।